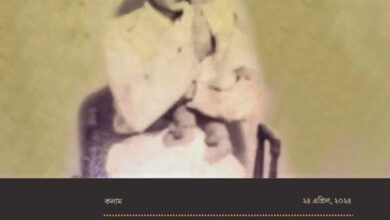স্বাচ্ছন্দ্যেই বড় হয়েছি আমরা। পরিবারে অভাব বলে কিছু ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে গিয়েই প্রথম টের পাই না থাকার কষ্টটা। খাওয়া নাই, রসদ নাই, পরিবারও কাছে নাই। বুঝলাম অভাব কাকে বলে। পাকিস্তানিদের চায়ের ইকোনমিটা শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করি আমরা। ইন্ডিয়া ছাড়া চা যেন আসতে না পারে। কলঘরে তৈরি হতো চা পাতা। তাই বাগানগুলোর কলঘর, সাহেবের বাংলো আর ব্রিজগুলো উড়িয়ে দিতাম।
একবার নির্দেশ আসে একটা মিশনে যাওয়ার। কি মিশন? বড়লেখাতে সাতমা ছড়া ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। পাঁচদিন আগে রেকি করা হলো। ছোট্ট দুটি নদী পাড় হয়ে যেতে হবে ওখানে। গাইড জানালো দুই নদীর ঘাটেই নৌকা রাখা থাকবে।
আমার সঙ্গে তেরোজন। সবার কাছে রাইফেল আর এক্সপ্লোসিভ। দুটো এসএলআরও ছিল। ক্যাম্প থেকে মুভ করি রাতে। লোকালয় এড়িয়ে পথ চলতাম। কুকুরগুলো যাতে ঘেউ ঘেউ না করে। এটা হলে রাজাকাররা টের পেয়ে যেত। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের চোখ এড়াতে অনেক অপারেশনেই সহযোদ্ধাদের সিগন্যাল পাঠাতাম ফানুস উড়িয়ে।
প্রথম নদীটির পাড়ে এসে নৌকা পেলাম। কিন্তু দ্বিতীয় নদীর কাছে কোনো নৌকা ছিল না। রাত তখন দুটো। নৌকার খোঁজে সহযোদ্ধারা আশপাশে ছুটে যান। কিন্তু না, কোনো নৌকা নেই। কী করবো ভাবছি। হঠাৎ আমাদের পেছনে একটা ঝোপে কি যেন নড়ে উঠলো। খানিক ভয় পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তাক করা হয়। কে ওখানে? কাঁপতে কাঁপতে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। বয়স তার পনের বা ষোল। পরনে শাড়ি। আচলের কিছু অংশ কামড়ে ধরে কাঁপছে। সিলেটি ভাষায় বলে– ‘মুক্তি নি? আমি জানতাম আপনারা আইবা।’
সে জানালো গ্রামে মুক্তিবাহিনী আসছে –এমন খবর পেলে পাকিস্তানি আর্মি এসে গোটা গ্রামটা জ্বালিয়ে দেবে। সেই ভয়েই গ্রামবাসী ঘাটের সব নৌকা ডুবিয়ে রেখেছে। ‘আও আমার লগে আও’ বলেই মেয়েটা নদীর এক পাশে ডুবানো নৌকাগুলো দেখিয়ে তুলে নিতে বলে। নিজেই খুঁজে আনে লগি। সহযোদ্ধারা পানি সেচে দুটি নৌকা নদীতে ভাসায়। মেয়েটি তখনও চারপাশ দেখছে আর ভয়ে কাঁপছে। তাকে সঙ্গে নিয়েই ওপারে যাই। একটি নৌকা ঘাটে রাখি। আরেকটি নৌকা নিয়ে মেয়েটি নদীর জলের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। পুরো দৃশ্যটাই স্বপ্নের মতো মনে হয়।
ব্রিজটা উড়িয়ে ভোরের দিকে আমরা ক্যাম্পে ফিরি। মনের ভেতর তখনও ঘুরছিল মেয়েটির মুখখানা। গ্রামবাসীর চোখ এড়িয়ে, জীবনের ঝুঁকি জেনেও ওইরাতে সে এসেছিল শুধুই মুক্তিযোদ্ধাদের পার করিয়ে দিতে। এর চেয়ে বড় যুদ্ধ আর কি হতে পারে! তার নামটা জানা হয়নি, ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে পারিনি। সহযোদ্ধাদের কাছে মেয়েটি ছিল পরী বা ফেরেশতাহ। কিন্তু আমার কাছে সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু ওই মেয়েটি কি এখনও বেঁচে আছে? নাকি সে ধরা পড়ে গিয়েছিল? তাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে? বেঁচে থাকলে ওর কি বিয়ে হয়েছে? তার ছেলেমেয়েরা কি জানে তার মা একজন ফ্রিডম ফাইটার?
মেয়েটিকে নিয়ে এমন হাজারো প্রশ্ন আজও ঘুরপাক খায় মনের অতলে। ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাসটাও তুলে আনতে হবে খোকন। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হবে না। একাত্তরে এমন নারীরা পাশে ছিল বলেই মাত্র নয় মাসে আমার স্বাধীনতা পেয়েছি।
বুকের ভেতর দাগ কেটে থাকা যুদ্ধদিনের একটি ঘটনা এভাবেই তুলে ধরেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আহম্মদ বাবু।
সবাই ডাকে– রুহেল আহমেদ। কিন্তু তিনি অধিক পরিচিত ‘মুক্তি বাবু’ নামে। মুক্তিযুদ্ধের কাগুজে সনদ নেননি তিনি। তার মতে– ‘মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদন করে কেন সনদ নিতে হবে। বরং রাষ্ট্রেরই উচিত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ ঘরে পৌঁছে দেওয়া।’ তিনি পান না কোনো যুদ্ধাহত ভাতাও। ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের যোগ দেওয়ার পূর্বে চার নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাব সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই যোদ্ধা। কিন্তু অফিসিয়ালি সেই তথ্যটিও লিপিবদ্ধ হয়নি কোথাও। তবে এ নিয়ে কোনো খেদ নেই তার। স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন– তাতেই তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। সম্ভবনাময় বাংলাদেশ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী এই বীর। এক বিকেলে তার বাড়িতে বসেই দীর্ঘ আলাপ চলে দেশ ও যুদ্ধদিনের নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে।

দুই ভাই ও দুই বোনের সংসারে রুহুল আহম্মদ বাবুু দ্বিতীয়। বাবা নুরু-উর-রহমান আর মায়ের নাম আসমা রহমান। আদি বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি গ্রামে। বাবা সেন্ট্রালে এসে পলিটিক্স করবেন। তাই সিলেট থেকে পরিবারসহ চলে আসেন ঢাকায়। বসতি গড়েন ধানমন্ডির সাত নম্বর রোডের এগারো নম্বর প্লটে (পুরাতন ১৮/বি)।
রুহুল আহম্মদের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি সিলেট গভমেন্ট স্কুলে। ঢাকায় এসে প্রথমে ভর্তি হন পলিট্যাকনিক হাই স্কুল এবং পরে ধানমন্ডি গভমেন্ট স্কুলে। ১৯৬৬ সালে তিনি মেট্রিক পাশ করেন। এরপর জগন্নাথ কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট শেষ করে ভর্তি হন বুয়েটে, আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।
আলাপচারিতার শুরুতেই শুনি পারিবারের কথা। তার ভাষায়–
‘আব্বা সিলেট আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে যুক্তফ্রন্ট থেকে নমিনেশন নিয়ে নির্বাচন করেন। পাকিস্তানের সেন্ট্রাল মিনিস্টার হয়ে তিনি যখন করাচি চলে যান তখন সিলেট আওয়ামী মুসলিম লীগের হাল ধরেন দেওয়ান ফরিদ গাজী ও ধলা ভাই। সিলেট ছাত্রলীগও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের বাড়িতে, নয়াসড়কে।
রাজবন্দী হিসেবে আব্বা জেল খেটেছেন বারো বার। বাড়িতে সবাই মিলে দাবা খেলতাম। হেরে গেলেই তিনি বলতেন–‘এবার জেল থেকে ঘুরে এসেই তোদের হারাব।’ কেন্দ্রীয় নেতারা সিলেটে আসলে আমাদের বাড়িতেই উঠতেন। একবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও এসেছিলেন। ছোটবেলায় তার কোলে বসেছি, ভাসানী আর শেখ সাহেবের কোলে ওঠার সৌভাগ্যও হয়েছিল। পরবর্তীতে আব্বা ভাসানী ন্যাপে চলে যান। কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে কখনও পিছপা হননি। এভাবে একটা রাজনৈতিক আবহে বড় হয়েছি আমরা।’
বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণই স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ডিক্লিয়ার বলে মনে করেন রুহুল আহম্মদ বাবু। তিনিও উপস্থিত ছিলেন রেসকোর্স ময়দানে। ওইদিনের স্মৃতিচারণ করলেন ঠিক এভাবে– ‘আগেই খবর পাই রেসকোর্স ময়দানে মিটিং হবে। ধরেই নিয়েছিলাম শেখ মুজিব স্বাধীনতা ডিক্লিয়ার করবেন। আব্বা তখন ভাসানী ন্যাপের চেয়ারম্যান। তিনিসহ আমি, ছোটভাই সোহেল আহমেদ, বন্ধু আইয়ুব খান ও মাহবুবুর রহমান সেলিম চলে যাই রেসকোর্সে। খুব কাছ থেকে শুনি ঐতিহাসিক ভাষণটি। বঙ্গবন্ধু পরিস্কারভাবে বললেন– ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।’ এরপরও কি স্বাধীনতা ডিক্লিয়ার করণ লাগে? এর চেয়ে আর কত সোজা বাংলায় বঙ্গবন্ধু বলবেন। স্মরণকালের বেস্ট স্পিচ এটি। অথচ বিএনপির লোকেরা এখনও কয় ঘোষণা নাকি জিয়া করছে। আরে স্বাধীনতার ঘোষণা তো মার্চের সাত তারিখেই হয়ে গেছে।’
বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে ইকবাল হলের (বর্তমানে জহিরুল হক হল) পানির ট্যাকিংর মাঠে ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেন ছাত্রনেতারা। রুহুল আহম্মদ বাবু সেখানে ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং করেন। ওই রাইফেলটা সঙ্গেই রাখতেন সবসময়। ইউনাইটেড ব্যাংক অব পাকিস্তানের অফিস থেকে একটি জিপ নেন তারা। ধানমন্ডিতে যেন অরাজকতা আর লুটপাট না হয় সে কারণে একটা টিম করে রাতভর পাহারা দিতেন। এ কাজে তাদের নেতৃত্ব দেন পানাউল্লাহ সাহেবের ছেলে খোকন। শেখ কামালের সঙ্গেও তাদের লিয়াজো ছিল।

কিন্তু ২৫ মার্চ রাতেই শহীদ হন তাদের খোকন ভাই। কীভাবে? সে ইতিহাস শুনি রুহুল আহম্মদের জবানিতে। তার ভাষায়– ‘ওইদিন সন্ধ্যায় সিরাজ নামে একজন এসে বলে– ‘বাবু, আজ রাতে আর্মি নামবো। যেভাবে পারছ ব্যারিকেড দে।’ কলাবাগান লেকের পাশে বড় একটা গাছ ছিল। এলাকার লোকজন নিয়া আমরা ওই গাছ কেটে রাস্তায় ফেলি। মনে তখন অন্যরকম স্পিরিট। গাছের ব্যারিকেড দিয়াই ট্যাংক থামামু। কোন ধারণাই ছিল না আমাদের। মনে ছিল শুধু দুর্বার সাহস।
ঢাকা কলেজের উল্টো দিকে চিটাগাং হোটেল। সেখানে বসে বুনদিয়া আর পরোটা খাচ্ছি। সঙ্গে মাহবুবুর রহমান সেলিম, আইয়ুব খান, আমার ছোট ভাই আর খোকন ভাই। রাত তখন আনুমানিক ১১টা। হঠাৎ গুলির শব্দ। খোকন ভাই উত্তেজিত হয়ে বললেন– ‘ধানমন্ডিতে কে গোলাগুলি করে? বাবু চল তো, শেখ সাহেবরে পাহারা দিমু। কোন শালায় আসে দেহি।’ কী ইমোশন আর মনোবল দেখেন। আমাদের ধারণাতেই নাই যে পাকিস্তানিরা নাইমা গেছে।
ওরা দুই নম্বর রোড দিয়ে এগুচ্ছিল। আমাদের জিপের সামনে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগানো। বনেটের ওপর আমি বইসা আছি ওই ডামি রাইফেলটা নিয়া। পথে পাকিস্তানিদের সাজোয়া গাড়িগুলো সাইড দেয়। ওরা ভাবছে কোনো আর্মি অফিসারের গাড়ি হবে। আমরা দ্রুত কলাবাগানের বসিরউদ্দিন রোডে যাই। ছায়ানটের অফিস ছিল ওখানে। সেখানেই গাড়িটা রাখি।
বুঝে যাই কিছু একটা ঘটবে। পান্থপথে তখন ধানমন্ডি লেকেরই একটা ডোবা ছিল। সেটা পার হয়ে ওপারে শেখ সাহেবের বাড়িতে যাব। এমনটাই পরিকল্পনা। রাস্তার পাশে ডোবার আড়ালে লুকিয়ে আমরা। প্রথম খোকন ভাই দৌড়ে রাস্তা পার হন। ওপারে গিয়ে হাতের টর্চটা জ্বালাতেই অজস্র গুলির শব্দ। কি হলো? দেখলাম তিনি মাটিতে পড়েই ছটফট করছেন। এক সময় তা নিথর হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। আর্মিদের দুইটা জিপ আসে। তার মুখে ওরা লাইট মেরেই বলে–‘শালা মার গিয়া’। তখনই রিয়েলাইজ করলাম– ‘হোয়াট দা হেল’। আমরা যা করতে যাচ্ছি তা তো ছেলেখেলা নয়।
রাতেই লুকিয়ে বাসায় ফিরলাম। শরীরটা তখনও কাঁপছে। খোকন ভাইয়ের জন্য বুকের ভেতর চাপা কষ্ট। কারফিউ উঠলে আমরা লাশের খোঁজে বের হই। ওরা লাশটা সোবহানবাগ মসজিদের বারান্দায় ফেলে রেখেছিল। হাতটায় তখনও টর্চ লাইট ধরা। গুলিতে আরেক হাত উড়ে গেছে।
লাশ নিয়ে ধানমন্ডি সাত নম্বরে খোকন ভাইয়ের বাড়ি হয়ে আজিমপুর গোরস্থানে যাই। বিভিন্ন জায়গা থেকেও তখন আসছে শত শত লাশ। পরিচিত কয়েকজন বলল এখানে থাকা নিরাপদ নয়। তাই দাফনের জন্য লাশটা দিয়েই চলে আসি।’
এরপর আপনারা কী করলেন?
‘বাড়ি ফিরতেই আম্মা বললেন যুদ্ধে যাও। পায়ে হেঁটে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে যুক্ত হন বন্ধু মাহবুবুর রহমান সেলিম, আইয়ুব খান ও ছোট ভাই সোহেল। নরসিংদী থেকে ব্যাক করে আইয়ুব। সে পরে বামদলের গেরিলা বাহিনীতে চলে যায়। সিলেট পৌঁছালে ছোট ভাই সোহেলও গ্রামে থাকে। পরে সে মুক্তিযুদ্ধ করে দুই নম্বর সেক্টরে, মেজর এটিএম হায়দারের অধীনে। শুধু মাহবুবুর রহমান সেলিমসহ আমরা জকিগঞ্জ হয়ে চলে যাই ভারতের করিমগঞ্জে।
ওখানেই রিক্রুট করা হচ্ছিল। লাইনে দাঁড়াই। হঠাৎ একজন এসে বলে– ‘আপনি তো নুরুর রহমান সাহেবের ছেলে। আপনাকে নেওয়া যাবে না।’ কেন? আপনার বাবা ওসমানী সাহেবের অ্যাগেইনেস্টে নির্বাচনে দাঁড়াইছিল। আমি বলি– ‘উনি তো ন্যাপ থেকে নির্বাচন করেছেন। মুসলিম লীগ তো করেননি।’ ওরা কোনো কথাই শুনলো না। দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকি।

বাছাই করে ওরা সবাইরে ভাঙ্গাচোরা একটা বাসে তুলে দেয়। সেটা কাছে আসতেই লাফিয়ে উঠে পড়ি। এভাবে পৌঁছি লোহারবনে। কয়েকদিন পরেই আসেন ক্যাপ্টেন চৌ (চৌধুরী)। বড় বড় ট্রাকে সবাইকে তুলে নেয়। অতঃপর খাসিয়া জোনসের হিল পেরিয়ে চলে আসি আসামের ইন্দ্রোনগর ট্রেনিং ক্যাম্পে। এখানে সব বিবেচনায় ওরা ক্যাপ্টেন অব দা ক্যাম্প হিসেবে আমায় সিলেক্ট করে।
ট্রেনিং কি খুব সহজ ছিল?
রুহুল আহম্মদের উত্তর–‘কষ্টের ছিল। সকাল বেলা পাহাড় থেকে নেমে এক মগ চা আর দুইটা পুরি খেতাম। আবার উঁচু পাহাড়ের উপর উঠতে হতো। সারাদিন চলত বন্দুক ও এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং। সন্ধ্যায় তাবুতে ফিরেই গা হেলিয়ে দিতাম। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকে ট্রেনিং থেকেও পালিয়েছিল। আমাদের তো ফিটনেস ছিল না। কিন্তু মনোবলটা ছিল প্রবল। সে কারণেই টিকে গেছি।
প্রথমে থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এসএলআর, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, গ্রেনেড থ্রো প্রভৃতি শিখি। মনে পড়ে ওস্তাদ হারবাং সিংয়ের কথা। উনি ছিলেন সরদারজি, পাঞ্জাবের লোক। ট্রেনিংয়ের শেষের দিকে পরিদর্শনে আসেন কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী। আমি তখন ভয়ে। এই বুঝি ক্যাপ্টেনশিপ চলে যায়। কিন্তু না। তেমনটি ঘটল না। পরিচয় পেয়েই উনি জড়িয়ে ধরে বললেন– ‘নুরু ভাইয়ের ছেলে চলে আসছো। ভেরি গুড।’ ট্রেনিংয়ে আমার এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নম্বর ছিল ৩৯৯।’
ট্র্রেনিং শেষে রুহুল আহম্মদ বাবুকে কমান্ডার করে পাঠানো হয় চার নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কুকিতলে। তার অধীনে ছিল প্রায় ছয়শ মুক্তিযোদ্ধা। যার মধ্যে পঁচানব্বই জনই গ্রামের সাধারণ কৃষক, চাষা আর ছাত্র। তিনি যুদ্ধ করেছেন– বড়লেখা, ছোটলেখা, জুড়ি, দিলখুশা চা বাগান, লাঠিটিলা, সোনারুপা চা বাগান, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি এলাকায়।
এক অপারেশনে মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত হন এই বীরযোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনাদের সাবমেশিন গানের গুলিতে তার বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচের হাড় উড়ে যায়। হাঁটুর ওপরেও লাগে মর্টার শেলের স্প্রিন্টার।
কী ঘটেছিল রক্তাক্ত ওই দিনটিতে? জানতে চাই আমরা। উত্তরে মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আহম্মদ বাবু বলেন সেদিনের আদ্যোপান্ত। তার ভাষায়–

‘সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের কথা। জেনারেল কাপুরসহ ইন্ডিয়ান আর্মিরা আসে ক্যাম্পে। বলে– ইউ আর রেডি টু মেজর অ্যাটাক। কি সেটা? দিলখুশা চা বাগানে আছে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প। এক কোম্পানিতে ১২৫ জনের মতো। ওটা দখলে নিতে হবে। আর্টিলারি সার্পোট দেবে ইন্ডিয়ান আর্মিরা। হিট করা আগেই রপ্ত করেছি আমরা। লাস্ট অ্যাটাক করবে অ্যাসল্ট পার্টি। কিন্তু ফার্স্ট অ্যাটাকে যাবে কাট অফ পার্টি। আরেকটা থাকবে কাভার পার্টি।
ওখানে ঢোকার দুটি ব্রিজ ছিল। পরিকল্পনা হয় কাট অফ পার্টি ব্রিজ দুটি উড়িয়ে বসে থাকবে। রাতু ও জুড়ির দিক থেকে ঢুকতে দেবে না কাউকে। বেরুতে গেলে তারাও অ্যাটাক করবে। কাভার পার্টি টিলা টু টিলা ফায়ারিং করতে থাকবে। এরপর অ্যাটাক করবে অ্যাসল্ট পার্টি। এরা নিচের দিকে পজিশনে থেকে কাভার পার্টির গুলির মধ্যেই অ্যাডভান্স হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কার দখলে নেবে। এরপর চলবে হ্যান্ড টু হ্যান্ড ফাইট। ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে, আর্টিলারিতে। পুরো অপারেশনের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।
সন্ধ্যায় মুভ করে ভোরে গন্তব্যে পৌঁছি। আমরা প্রায় দেড়শ জন। আমি অ্যাসল্ট গ্রুপে। পজিশন নিয়ে বসে আছি। একটা রাউন্ড আর্টিলারি ফেলা হলো। ধুম করে শব্দ হয়। এক, দুই, তিন করে একুশ পর্যন্ত গুনতেই ক্রমাগত আর্টিলারি পড়তে থাকে। প্রথম আর্টিলারিটা পড়ে মেইন কলঘর থেকে একটু সামনে। পাকিস্তানি সেনারা চিৎকার দিয়ে বলে– ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার।’
আর্টিলারি ফেলা শেষ। ভোর তখন চারটা। ধুম করে একটা শব্দ হওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই আরেকটা শব্দ হলো। ধরে নিই কাট অফ পার্টি দুটি ব্রিজই উড়িয়ে দিয়েছে। এখন কেউ আর ঢুকতে পারবে না। ছয়জন করে ওই গ্রুপের একটাতে লিয়াকত অন্যটিতে ছিল রফিক।
এরপরই কাভার পার্টি ফায়ার আরম্ভ করে। তুমুল গোলাগুলি চলছে। অ্যাসল্ট পার্টি তখন প্রস্তুত। ডানে ছিল আতিক। ওয়াবদার ড্রাইভার, বিয়ানীবাজার বাড়ি। বাম দিকে খায়ের। সঙ্গে আরও দশ বারোজন। সবাই স্থির হয়ে থাকে। কাভার পার্টির গুলি শেষ হলেই– উই হ্যাভ টু অ্যাটাক। বাগানের মাটিতে শুয়ে আছি। প্রথম কেউ উঠছিল না। আতিক গুলি শুরু করে। আমি ‘জয় বাংলা’ বলে আগে বাড়ি। তিনটি গ্রুপে অ্যাটাক করে ওদের বাঙ্কার দখলে নিই। তখনই বাঁ পায়ে হাঁটুর ওপরে এসে লাগে মর্টার সেলের ছোট্ট একটি স্প্রিন্টার। রক্ত পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গামছা দিয়ে জায়গাটি বেঁধে দিই।
থেমে থেমে গোলাগুলি চলছে। ওরা সাহেবের বাংলোর দিকে। ভোর তখন ৬ টার মতো। হঠাৎ শুনি গুম গুম শব্দ। কিসের শব্দ? দেখি চা বাগানের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি সাজোয়া বাহিনীর একটা দল আসছে। ওদের ট্রাকে মেশিন গান ফিট করা।
তখনই বুঝে যাই পুরোপুরি কাট অফ হয়নি এলাকাটি। আসলে একটা গ্রুপ পৌছাতেই পারেনি ব্রিজে। কারণ ব্রিজটা অ্যাম্বুস করে রেখেছিল রাজাকাররা। কিন্তু সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আরেকটা গ্রুপ লম্বা ব্রিজ হওয়ায় দুইটা এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেছিল। ফলে শব্দ হয় দুটি। যা শুনে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম কাট অফ হয়েছে।
সাজোয়া বাহিনীর সামনে আমরা টিকতে পারব না। তাই রেড ফায়ার করি। মানে– ‘উইড্রো’। দৌড়ে সরে যাচ্ছি। হাতে স্টেনগান। সঙ্গে তিনটা গ্রেনেড। হঠাৎ গুলির শব্দ। টিলার ওপর ছোট্ট একটা বাঙ্কার ছিল, খেয়াল করিনি। সেখান থেকে সাবমেশিনগানের গুলি আসতে থাকে। ছিটকে পড়ে যাই গর্তে। প্রথম কিছুই টের পাইনি। বাঁ পাটা পুরো ব্যাকে গিয়ে হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে যাই। হাঁটুর নিচ থেকে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছিল। খানিক পরেই শুরু হয় প্রচণ্ড ব্যাথা।
হাত দিতেই অনুভব করলাম চামড়ার সাথে বাঁ পা-টা লেগে আছে কোনরকমে। গুলি লেগে হাঁটুর নিচে গোড়ালির ওপরে হাড়ের কিছু অংশ উড়ে যায়। ওই অবস্থায় চা বাগানের ভেতর পা টেনে টেনে এগোই। মনে হয়েছিল জীবনটা বেরিয়ে যাবে। টিলার ওপর উঠেই উল্টো দিকে গড়িয়ে পড়ি। পুরো পা তখন রক্তে মাখা। সেই রক্তে লেগে আছে অসংখ্য শুকনো বাঁশ পাতা।
মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছিলাম। মাশুক নামে একটা ছেলে আসে। তাকে বলি–‘তোমরা সরে যাও। আমি ঠেকাই।’ ক্রমেই চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে। একটা মইয়ের ওপর চাটাই ফেলে তার ওপর শুইয়ে সহযোদ্ধারা আমাকে তুলে নেয়। প্রথমে কুকিতলে এরপর চিকিৎসা হয় মাসিমপুর মিলিটারি হাসপাতালে।’
স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য রুহুল আহম্মদ বাবুকে সরকারিভাবে পাঠানো হয় ইস্ট জার্মানিতে। চিকিৎসা হয় ক্রাংকেন হাউজ বুখ, ইস্ট বার্লিনে। পায়ের হাড় গ্রাফটিং করা হয় ওখানেই। পঁচিশ জনের দলে শমসের মবিন চৌধুরী, আমিন আহমেদ চৌধুরী, জেনারেল হারুনেরও চিকিৎসা হয় সেখানে।
১৯৭১-এ ঢাকার গেরিলাদের সম্পর্কে এই যুদ্ধাহতের মূল্যায়নটি এমন– ‘মেইনলি দুই রকম যুদ্ধ হইছে। একটা হচ্ছে আরবান গেরিলারা যারা ইনডাকসনে ছিল। যেমন ঢাকায় ক্র্যাক প্লাটুন। এরা ছোটখাট ঘটনা ঘটায়া গরম রাখতো। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ও পাক মটরে (বাংলামটর) বোম মেরে শহরের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকতে হতো তাদের। আমাদের মিশন ঢাকার মতো টাফ ছিল না। লম্বা পথ পেরিয়ে হয়তো অপারেশন করতাম। কিন্তু ফিরে এসে সেইফ জোনেই থাকতাম। কিন্তু ঢাকার গেরিলারা সেইফ ছিল না। ওদের সবসময়ই রিক্সে থাকতে হতো।’
যে দেশের জন্য রক্ত দিলেন সেই দেশ কি পেয়েছেন?

চোখেমুখে আলো ছড়িয়ে এই বীরের উত্তর–‘ডেফেনেটলি পেয়েছি। সাইথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের জিডিপি হায়েস্ট। আমি সবসময় বলি ফ্যান্টাস্টিক আছি। শুভদিন আসছে না, এসে গেছে। যতদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নেতৃত্বে থাকবে এই দেশ এগোবে। এটা আমার বিশ্বাস। যেই পাকিস্তানিগো আমরা লাত্থি দিয়া ফালায়া দিছি। সেই পাকিস্তান এখন কয়– ‘ইস্ট পাকিস্তান চালা গিয়া।’ আমরা চইলা গেলাম কই। তুম লোক ভাগা। আমরা মেজরিটি। মেজরিটি কখনও চলে যায় না।’
আপনাদের স্বপ্ন কী ছিল?
‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন। জাতির পিতা সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে বলেছিলেন– ‘আমি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা বীজ পুতে রেখে গেলাম। এই বীজ যেদিন উৎপাটন করা হবে, সেদিন বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকে শেখ হাসিনা সেই জাতির পিতার মেয়ে। আর আমি এদেশের হারিয়ে যাওয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা। যখন দেখি মন্দির ভাঙা হচ্ছে। এয়ারপোর্টের সামনে লালনের ভাস্কর্য ভাঙা হয়েছে। যখন দেখি শুধু কোরআন তেলওয়াত করেই অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। গীতা, ট্রিপিটক পাঠ করা হচ্ছে না। তখন কষ্ট লাগে। তাহলে আমরা কি বঙ্গবন্ধুর কথা মানছি? আমি দেখতে চাই না– তুমি হিন্দু কি মুসলমান। দেখতে চাই, তুমি মানুষ কিনা। তুমি বাংলাদেশকে ভালবাস কিনা। তুমি বাঙালি কিনা।’
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের ভূমিকা অতুলনীয় ছিল বলে মনে করেন এই সূর্যসন্তান। তার ভাষায়– ‘গণজাগরণ মঞ্চ না হলে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি হতো না। ওখানে আমরাও গিয়েছিলাম। কিন্তু মঞ্চে উঠিনি। সবার একটা সময় থাকে। ওটা ছিল ইমরান, লাকী আর পিয়ালদের সময়। তাই গণজাগরণ মঞ্চের কথা ইতিহাসে লিখতেই হবে।’
দেশ কেমন চলছে?
এ যোদ্ধা অকপটে বলেন– ‘দেশ নিয়ে আমি এক্সসাইটেড। হ্যাঁ, কিছু ভুল হচ্ছে। কিন্তু পজেটিভ জিনিসও তো হচ্ছে। পদ্মা ব্রিজ তো বানায়ে ফেলছে। ভুলের সাথে ভালটার কথাও বলতে হবে। তবে প্রফেসার ইউনুসকে কাজে লাগানো উচিত ছিল। বিদেশের মাটিতে যদি একশবার বাংলাদেশের নাম শুনে থাকি তাহলে আটানব্বই বারই শুনেছি গ্রামীন ব্যাংক আর ইউনুসের কারণে।’
ছাত্র হত্যা নিয়ে বুয়েটের এই সাবেক ছাত্র বলেন– ‘বুয়েটের ইতিহাসে এটা কলঙ্কিত ঘটনা। আমি বলব এটা ‘পাওয়ার করাপশন’। আওয়ামী লীগ তিন টার্ম ক্ষমতায়। ফলে দলে প্রচুর আগাছা তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগের আগাছা কিন্তু মূল গাছটাকে বাড়তে দিবে না। তাই ছাত্রলীগ বলেন আর যুবলীগ বলেন, গুন্ডামি আর নোংরামি বন্ধ করতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা উঠছে। এটা ঠিক হবে না। আব্বা বলতেন, সকল নীতির উর্ধ্বে রাজনীতি। তাই রাজনীতি খারাপ না। খারাপ হয় রাজনৈতিকরা। ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন। সেটা তো খারাপ নয়। নিজেদের স্বার্থে কিছু লীগার সেটাকে কলুষিত করছে। তাদের শক্ত হাতে দমন করতে হবে। তবে রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তিক ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।’
আজ একটা ইয়াং ছেলে ব্যাংক আর বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায়। গার্মেন্টেসে নাম্বার ওয়ান আমরা। নতুন প্রজন্ম সোনার বাংলা বাজলে দাড়িয়ে কান্দে। তাই প্রজন্মকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আহম্মদ বাবু। তাদের উদ্দেশেই তিনি বললেন শেষ কথাগুলো– ‘আমরা নয় মাসে খুব সোজা একটা কাজ করে গেছি। দেশটাকে স্বাধীন করেছি। এর চেয়ে হানড্রেড টাইমস কঠিন হচ্ছে দেশটাকে গড়া। তোমাদের নয় বছর না, নব্বই বছর দিলাম– দেশটাকে গড়ো। তোমরা ঠিক পথে আছো। শুধু দেশটাকে ভালবেসো।’

সংক্ষিপ্ত তথ্য
নাম: যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আহম্মদ বাবু।
ট্রেনিং: আসামের ইন্দ্রোনগর ট্রেনিং ক্যাম্পে। এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নম্বর ৩৯৯।
মুক্তিযুদ্ধ করেছেন: চার নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাব সেক্টরের আওতাধীন বড়লেখা, ছোটলেখা, জুড়ি, দিলখুশা চা বাগান, লাঠিটিলা, সোনারুপা চা বাগান, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি এলাকায়।
যুদ্ধাহত: একাত্তরের সেপ্টেম্বরে, প্রথম দিকের ঘটনা। দিলখুশা চা বাগান অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের সাবমেশিন গানের গুলিতে তার বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচের হাড় উড়ে যায়। হাঁটুর ওপরেও লাগে মর্টার শেলের স্প্লিন্টার।
ছবি: সালেক খোকন
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ১৫ অক্টোবর ২০১৯
© 2019, https:.